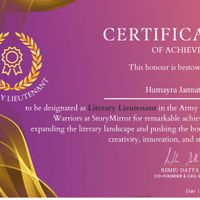ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু 2
ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু 2


বাঘা-যতীন(যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) :
-“১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজদের সঙ্গে সশস্ত্র সম্মুখযুদ্ধে মারা যান যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন।”
মাধ্যমিকের ইতিহাস বইতে সাকুল্যে তিন-চারটি লাইন বরাদ্দ ছিল দেশের বীর সন্তান বাঘা যতীনের উদ্দেশ্যে। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে, জানা নেই ইত্যবসরে নতুন কোনকিছু সংযুক্ত হয়েছে কিনা, নাকি বিয়োজন হয়েছে, কিন্তু আজ থেকে কুড়ি বছর আগের পাঠক্রমে এটুকুই বরাদ্দ ছিল ছাত্রদের জন্য। এটিই ছিল বাঘা যতীনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ।
অবশ্য আমাদের অস্থিমজ্জাগত উদাসীনতার আরও কিছু বিচিত্র উদাহরণ এই প্রসঙ্গে তুলে ধরবার লোভ সামলাতে পারছি না; ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’ বাকিগুলি আপনারাই পাদপূরণ করে নিন-
-“ইতিহাস? তা জেনে কি হবে? কে কবে কোথায় কি করছিলেন তা জেনে লাভ কি?”- হবে হয়তো! আচ্ছা, তীর সামনের দিকে যাওয়ার আগে একটু পেছিয়ে আসে না?
-“বাঘা-যতীন? মানে…যিনি অনশন করেছিলেন?”- সব্বোনাশ! এ তো উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে এসে পড়ল!
-“বাঘা-যতীনকে চিনব না? যতীন ব্যানার্জী সম্পর্কে পড়েছি তো… ঐ তো… কি যেন বলে…নিরাবলম্ব স্বামীর কথা বলছেন তো!”- ম্যাঁও সামলাও!
-“হ্যাঁ, জানি। উনি খালি হাতে বাঘ মেরেছিলেন এটা জানি।”- ও, তা খালি হাতে বাঘ মেরেছিলেন বলেই ওঁনাকে তার মানে লোকে মনে রেখেছিলেন, ইঙ্গিত তো সেদিকেই।
উপরিউক্ত কথোপকথনগুলি কাল্পনিক নয়, আর বক্তারাও ফেলে দেওয়ার মত, বা উপেক্ষা করবার মত পাত্র-পাত্রী নন। আরও রকমারি, রংবাহারি পর্ব ছিল, কিন্তু এ নিয়ে আর চর্বিতচর্বণ না করাই ভালো।
তার থেকে একটি খুব সাধারণ প্রশ্ন করা যাক- যদি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী খালি হাতে বাঘ না মারতেন, বা কোন যান-বাহনে না চড়ে মাইলের পর মাইল অনায়াসে পায়ে হেঁটে অতিক্রম না করতেন, বা কোন গোরা সৈন্যকে মানবিকতার প্রশ্নে আড়ং ধোলাই না দিতেন, তাহলে কি তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি কি ব্রাত্য হয়ে যেতেন? ক্ষেত্রবিশেষে শক্তির প্রয়োগ আবশ্যিক, কিন্তু নীতিবিহীন শক্তির প্রয়োগ তো বর্বরতা! তাহলে কি সেই কারণ যার জন্য আমরা তাঁকে স্মরণ করব?
চকচক করলেই সোনা হয় না বটে, কিন্তু সোনা চেনা যায় কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য দিয়েই।
বাঘাযতীন চরিত্রটির মূল ভিত্তি অকুতোভয়তা, দুঃসাহস ও ভীতিহীনতা; আর এই দুঃসাহসের ভিত্তি কিন্তু অনেক ছোটবেলা থেকেই।
নদীয়ার কুষ্টিয়া জেলার কয়াগ্রামে কোন এক দিন সকালে এক গৃহস্থ বাড়িতে রান্না করছেন মা; বাইরে খেলা করছে তাঁর ছয়-সাত বছরের ছেলে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, পাংশু, বিবর্ণ মুখ করে ছেলে ঘরে ঢুকে পড়েছে।
-“কি হয়েছে রে, জ্যোতি?”- জিজ্ঞাসা করলেন মা।
-“একটা কুকুর, মা! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে বারবার আমার দিকে।”
-“কুকুর? লজ্জা করে না একটা খেঁকি কুকুরের ভয়ে ঘরে ঢুকতে? এই নে, ধর।”
একটি বড় আকারের চ্যালাকাঠ উঠে এল ছেলের হাতে।
-“যা। এটা দিয়ে ভালো করে কুকুর মেরে আয়” – আদেশ দিলেন মা। ছেলেও তৎক্ষণাৎ দৌড়ল আদেশ পালন করতে। কুকুর কি তখন আর বসে থাকে সেখানে? ছেলের হাতে চ্যালাকাঠ দেখেই সে কুকুর তখন দৌড়ে পগার-পার!
-‘বাঘা-যতীন’, লেখক- ডাঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ভয়কে জয় করবার শিক্ষাটা যে অনেক প্রাচীন, এবং অনেক গভীরে প্রোথিত। এর পূর্ণ বিকাশ কিন্তু শুধু কুকরি হাতে বাঘ মারবার ঘটনার মধ্য দিয়ে নয়, এই সাহসের শিকড় আরও গভীরে। বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল; কিন্তু মৃত্যু আসে নি। পরিবর্তে এসেছে অমরত্ব; অন্য দিক দিয়ে।
এখানেই প্রশ্নটি আবার উঠছে; বাঘ না মারলে বাঘা যতীন কি ‘বাঘাযতীন’ হয়ে উঠতে পারতেন না? এই ঘটনা তাঁর অসীম শারীরিক শক্তিকে প্রমাণ করে মাত্র, কিন্তু তা তো কারোর যোগ্যতা নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। তাহলে কি সেই গুণ, যা তাঁকে আলাদা করে সমকাল থেকে?
তাঁর ভাবশিষ্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়)-এর একটি ঐতিহাসিক উক্তি তুলে ধরি, তাহলে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে তাঁর চরিত্রের সার্থকতা-
-“Others were Great men, but he was a good man, and he will remain so unless we don’t realise that Goodness is essential to Greatness.”
তাঁর সবচেয়ে বড় চারিত্রীক গুণ- মনুষত্ব, যা একজন অচেনা রমণীকে ‘মা’ বলে ডাকতে শেখায়। বাঘ মারবার ঘটনাটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত, কিন্তু তাঁর ‘বাঘ’ শায়েস্তা করবার ঘটনাটি কিন্তু আরও বেশি অর্থবহ। তাও একটি নয়, একসঙ্গে চার-চারটি ব্রিটিশ বাঘ! এই ঘটনার মধ্য দিয়েই বোঝা যাবে, কতটা কর্তব্যবোধ, মনুষত্ব ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ভরে রেখেছিলেন তিনি; ব্যক্তি হিসেবে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীকে চিনতে সাহায্য করবে এই ঘটনা।
দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে ট্রেনে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন যতীন্দ্রনাথের এক সহযাত্রী, প্রবল জ্বর! শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌছে জল খেতে চাইলেন তিনি, গোটা বগিতে কারোর কাছে জল ছিল না। অগত্যা জল আনতে গেলেন যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং।
গোটা প্ল্যাটফর্মে তখন গিজগিজ করছে গোরা সৈনিক। ছুটি শেষে সকলেই তখন ফিরছেন কাজে। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না; তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে একটি কলে জল পেয়ে গ্লাসে জল ভর্তি করে নিলেন যতীন্দ্রনাথ। দিদি বিনোদবালার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অসুস্থ ব্যক্তি, ট্রেনের মধ্যে। দিদির কাছ থেকেই গ্লাসটি নিয়ে এসেছেন তিনি। জল ভর্ত্তি করে আবার নিজের বগিতে ফেরৎ আসছিলেন যতীন্দ্রনাথ।
ঠিক এই সময়টিতেই ঘটল একটি অঘটন। চারজন গোরা অফিসার গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্পে মশগুল ছিলেন একেবারে যতীন্দ্রনাথের বগির সামনেই; তাড়াহুড়োতে একজনের সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগল তাঁর। অফিসারটি কম কথার মানুষ, মুখে কোন শব্দ করলেন না,কোন বিরক্তিও না; স্রেফ হাতের ছড়িটি তুলে সশব্দে বসিয়ে দিলেন যতীন্দ্রনাথের পিঠে। একপলকের জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ, হয়তো যোগ্য একটি জবাব দিতে চাইছিলেন এই আচরণের। কিন্তু পথ আটকে দাঁড়াল পীড়িত রোগীর প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ। ফেরৎ চলে এলেন তিনি; জ্বর ও বিকারগ্রস্ত রোগীর মুখে তুলে দিলেন সেই জল। তারপর দিদি বিনোদবালার তত্ত্বাবধানে রোগীকে রেখে আবার ফেরৎ এলেন অকুস্থলে। চেপে ধরলেন বেত সমেত সামরিক অফিসারটির হাত।
-“মারলেন কেন?”
সামরিক অফিসারটি সম্পর্কে আগেই বলেছি- কম কথার মানুষ। আবারও কোন কথা না বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, ছড়ি তুলে মারতে গেলেন নিগারটিকে। কিন্তু এবার, পাল্টা একটি বিরাশি সিক্কার চড় মাথা ঘুরিয়ে দিল তাঁর; প্ল্যাটফর্ম আলো করে পড়ে রইলেন তিনি।
এবারে এগিয়ে এল দ্বিতীয় অফিসার, তারও একই দশা হল। তাকে মাটি ধরিয়েই তৃতীয়জনের দিকে পলকে ঘুরে গিয়ে বাঁ পায়ে এক সজোরে লাথি। যতীন্দ্রনাথকে আহত করবার জন্য সঙীন উঁচিয়ে ছিল সেই অফিসার; লাথি খেয়ে কুমড়ো-গড়ান গড়িয়ে গেল সে। তিন নম্বর ব্যক্তি ধরাশায়ী!
এর ঠিক আগেই ঘটেছিল সেই ঐতিহাসিক বাঘ মারবার ঘটনা, তার ক্ষত ডানপায়ে কিছুটা তখনও বয়ে নিয়ে বেরাচ্ছেন তিনি; একটু পা টেনে চলতে হয় তাঁকে। সেটা লক্ষ্য করেই চতুর্থ অফিসারটি বেয়নেট চালালেন তাঁর ডান পা লক্ষ্য করে। পা সরিয়ে নিয়েই সজোরে এক কীল বসালেন যতীন্দ্রনাথ, বীরপুঙ্গবের মাথায়! কাঁপতে কাঁপতে তিনিও বসে পড়লেন মাটিতে। চারজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার তখন পরাস্ত, ডাল-ভাতখাওয়া এক সাধারণ বাঙ্গালী যুবার হাতে, চেহারায় যাকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করা যায় না মোটেও!
ভারতবর্ষে তখন এক টালমাটাল অবস্থা। চতুর্দিকে ব্রিটিশরা তখন দিশাহারা। ব্রিটিশ রাজন্যবর্গ তখন পরপর আঘাতের ধাক্কায় বিপর্যস্ত। খয়ের খাঁ-দের অবস্থা সঙ্গীন। কিন্তু কে নেতৃত্ব দিচ্ছে, কে রসদ জোগাচ্ছে, কে পরিকল্পনা করছে- মূল মাথাটিকেই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! ঠিক এই সময়টিতে এই ঘটনাটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল- যতীন মুখার্জ্জী নামক এক সামরিক কর্মচারীর চারটি জাঁদরেল ব্রিটিশ অফিসারকে ধরে ঠ্যাঙানো। সামরিক অফিসাররা লোকলজ্জার ভয়ে যতীন মুখার্জ্জীর বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিল বটে, কিন্তু পুলিস হাত গুটিয়ে বসে থাকল না। চলল অনুসন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে পুলিসের নজরে এল যে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে চিংড়িপোতা রেল ডাকাতির আসামি নরেন ভট্টাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য যতীন মুখার্জ্জী অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ব্যারিস্টার বন্ধু জে.এন.রায়কে। এই বন্ধুটিকেই তিনি আবার নিয়োগ করেছিলেন ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলার আসামি কুঞ্জলাল সাহারায়ের হয়ে মামলা লড়তে। কানাঘুষোয় এও শোনা গেল, ‘ছাত্রভাণ্ডার’ ও ‘সমবায় সমিতি’ নামক দুটি স্বদেশী ভাণ্ডার চালান তিনি। এছাড়াও নন্দলাল ব্যানার্জ্জী ও আশু বিশ্বাস হত্যা এবং কার্জন-ওয়াইলি হত্যা প্রচেষ্টার পিছনে তাঁর আবছা ছায়া দেখতে পেল পুলিস। তক্কে তক্কে থাকল তারা, যতীন মুখার্জ্জীর বিরুদ্ধে পাকাপোক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টায়।
তাদের চেষ্টার পথ মসৃণ করে দেয় ডেপুটি পুলিস কমিশনার সামশুল আলম হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি। এই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিসি হেপাজতে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে সাধারণ জেরা, তারপর দৈহিক নির্যাতন, শেষে কৌশলে তাঁকে দিয়ে স্বীকার করানো হয় যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীই হলেন ষড়যন্ত্রের পিছনে মূল মস্তিষ্ক। যদিও যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে বন্দী করা যায় নি যতীন্দ্রনাথকে। বেকসুর খালাস হয়ে যান তিনি।
আঠেরো বছর বয়সী বীরেন্দ্র পুলিসি চালাকির কাছে ঠকে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করলেও, তাঁকে কিন্তু যতীন্দ্রনাথ আজীবন দেখেছেন সমবেদনার চোখে। বীরেন্দ্রর প্রতি অসূয়া হন নি তিনি মোটেও; বরং সর্বসমক্ষে তাঁর সাহসের প্রশংসা করে গেছেন আজীবন। কেউ তাঁর চরিত্রহানী করবার চেষ্টা করলেই প্রতিবাদে গর্জ্জে উঠেছেন যতীন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্রর প্রতি তাঁর এই ‘অবসেশন’-এর ব্যাপারটি ফুটে ওঠে একটি ছোট ঘটনায়-
রাসবিহারী তখন দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা মারবার ঘটনায় পলাতক; এই অবস্থাতেও একদিন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি- আশু ভবিষ্যত বিপ্লবের রূপরেখা নির্মাণে। জলে ভাসমান একটি ডিঙিতে আলাপচারীতা হচ্ছে দুজনের; তৃতীয় কোন সওয়ারী নেই তাতে। কথায় কথায় হঠাৎ বলে বসেন রাসবিহারী-
-“কিন্তু দাদা, বীরেন তো একজন ‘ট্রেইটর’, তার জন্যই তো আপনার এই সর্বনা-”
-“শাট আপ!”- বলে চীৎকার করে উঠলেন বাঘা যতীন; এত জোর যে নৌকো পর্যন্ত দুলে উঠল আচম্বিতে! বিষ্মিত রাসবিহারীকে এরপর পূর্বকথা বিবৃত করেন যতীন্দ্রনাথ; কিভাবে কৌশলে বীরেন্দ্রকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করিয়ে নেয় পুলিস।
সংগ্রামীর ‘ক্ষণিকের ভুল’ নয়, বৃহত্তর সাধনাকে স্বীকৃতি দিতেন যতীন্দ্রনাথ। উপরিউক্ত ঘটনাটি তারই একটি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। এটি তাঁর চরিত্রের অন্যতম বড় গুণ। সাধে কি তাঁর সম্পর্কে তাঁরই শিষ্যের মুখ দিয়ে বেরোয়- “কি গুণ করেছে দাদা শালা, ব্যাটাকে একটিবার না দেখে একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে পারি না!” এমনই চৌম্বকীয় আকর্ষক শক্তির উদাহরণ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ!
তবে ‘শাট আপ্’ শব্দের প্রয়োগ একবারই যে তিনি করেছিলেন জীবনে, তা কিন্তু নয়। এই শব্দযুগলের প্রয়োগ তিনি আগেও ঘটিয়েছেন, অন্যত্র। সেই কথাটিই এখন বলব।
একবার তাঁকে থানায় তলব করা হয়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তাঁকে বসানো হয় কাঠের টুলে, সামনে একটি ছোট, নীচু টেবিল। এগিয়ে আসেন বৃটিশ পুলিস অফিসার, যতীন্দ্রনাথকে ‘ক্রস’ করবার জন্য। নানারকম প্রশ্ন করা হয় যতীন্দ্রনাথকে; কৌশলে তা এড়িয়ে যান তিনি। ‘ক্রস’ করবার কায়দা পরিবর্তন করেন অফিসারটি; প্রথমে খানিক্ষণ ভীতি প্রদর্শন করেন তিনি, অবিচল থেকে মুচকি হেসে তা এড়িয়ে যান যতীন্দ্রনাথ। এতে কাজ না হওয়ায় শুরু হয় লোভ দেখানো। যতরকম কাঙ্খিত বাসনা জমা থাকে বস্তুতান্ত্রিক ব্রিটিশ হৃৎপিণ্ডে, সমস্ত কিছুই মেলে ধরেন ব্রিটিশ পুলিস অফিসারটি, যতীন্দ্রনাথের সামনে। এইবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল যতীন্দ্রনাথের, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একই কথা-
-“শাট আপ্!”
ছোট, নীচু টেবিলটি রাখা ছিল দুজনের মধ্যিখানে; গর্জ্জে ওঠবার সময় তাতে সজোরে দুইহাতে এক কিল বসালেন যতীন্দ্রনাথ; পরমুহুর্তেই কাঠের টেবিল মধ্যিখান থেকে ফেটে চৌচির! টেবিলের পরিণতি দেখে এরপর সেখানে আর দাঁড়াননি ব্রিটিশ বীরপুঙ্গব; গুটি গুটি পায়ে মানে-য় মানে-য় সরে পড়লেন তিনি। এরকম একটি রদ্দা তার পিঠে নেমে আসলে-
-“…He was a Good man…”
কুমোরখালির ঘটনা এই বাক্যটিকে, এই শব্দগুলিকে, এই বিশেষণকে বারংবার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করে। নরমে-গরমে একজন চরিত্র, যে সঠিক কারণে বলপ্রয়োগেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না। তারই একটি উদাহরণ কুমোরখালির ঘটনা।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের বিয়ে; কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তার মেয়ের উচ্চ, ধনী বংশে বিয়ে দেওয়ার জন্য। বিয়ের দিন বিধিব্যবস্থার তদারকি করতে গিয়ে হঠাৎ একটি বেয়াড়া বিষয় যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল। বরযাত্রীরা খাবার জিনিষকে খুব অপচয় করছেন- ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করছেন খাদ্যসামগ্রী। ‘ব্যাপারটা কি’ জানতে গিয়ে বেরিয়ে এল চমকপ্রদ তথ্য- সোনা-দানা ও অন্যান্য যৌতুক দেওয়া সত্বেও নগদ টাকার পরিমাণ কম হওয়ার সুবাদে বরযাত্রীদের তরফ থেকে এই হেনস্থা- খাবার নষ্ট করে অসহায়, গরীব পিতাটিকে একটু উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত।
-“অ, এই ব্যাপার? দাঁড়ান, দেখছি।”- যতীন্দ্রনাথের উত্তর। তাতে আশংকিত হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
-“ওদের কিছু কোরো না, বাবা! লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে নিয়ে এরপরে পথে বসতে হবে যে!”
-“তার থেকে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে গড়ুই-য়ের জলে ফেলে দিলেই তো পারতেন!”- যতীন্দ্রনাথের সপাট উত্তর। নীরব মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ পিতা।
একজন বন্ধুকে এবার যতীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিলেন কয়েকটি ছেলে জোগাড় করতে; তারা যেন লাঠি নিয়ে জড়ো হয় মণ্ডপের সামনে। তারপর নিজে গিয়ে ঢুকলেন খাওয়ার জায়গায়।
সেখানে তখন এক ছোকরা একটি চমচম নিয়ে তাগ্ করে ছুঁড়ে মেরেছে দেওয়ালের এক কোণে; পড়বি তো পর, সেটা হয়েছে যতীন্দ্রনাথের চোখের সামনে। ছোকরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।
-“ভাই, আমার সঙ্গে একটু আসুন তো, আপনাকে একটা দারুণ জিনিষ খাওয়াবো।”- এই বলে তাকে একপ্রকার জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন দেওয়ালের কোণে। সেখানে তখন ডাঁই করে পড়ে বিভিন্ন খাবার-দাবার। আবর্জনার মধ্যে। সেখানে ছোকরাকে দাঁড় করিয়ে যতীন্দ্রনাথ নোংরার দিকে দেখিয়ে বললেন-
-“ঐখানে কোথাও চমচমটা পড়ে আছে; ওটাকে তুলে মুখে পুরে নিন!”
-“অ্যাঁই চল রে! ভাড়াটে লোক নিয়ে এসেছে আমাদের অপদস্থ করবার জন্য। চল চল!”- এই বলে বরযাত্রীরা উঠেছে যেই, এমন সময়ে যতীন্দ্রনাথের লাঠিধারী বন্ধুরা সকলেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল মণ্ডপের ভিতর। বরযাত্রীদলের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। কারোরই আর জায়গা ছেড়ে নড়া হল না।
-“বৃদ্ধ, দরিদ্র লোক এত কষ্ট করে সব আয়োজন করেছে, কিছু না খেয়ে যাবেন কেন? যতটা খেতে চান, ততটাই পাবেন; কিন্তু কিছু নষ্ট হতে দেখলে কিন্তু আমরা তা সহ্য করব না। অ্যাঁই তোরা দেখিস, না খেয়ে যেন কেউ চলে না যায়, বরযাত্রী বলে কথা!”
-“আচ্ছা…দাঁড়াও! মেয়ের ওপর এর শোধ তোলা যাবে…!”- ভিড়ের মধ্য থেকে চাপাস্বরে বলে উঠল এক বীরপুঙ্গব।
-“তাই নাকি, মশাইয়ের ঘরে বুঝি মেয়ে-বৌ নেই?”- বক্তার দিকে তাকিয়ে বাঘের মত গর্জ্জে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ- “অন্যের বাড়ির মেয়ের ওপর বীরত্ব, তাই না? একটা কথা শুনে রাখুন, আমার বোনের ওপর যদি ওখানে কোন অত্যাচার চলে… আমি কিন্তু খোঁজ নিতে থাকব।”
‘সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ’- ডাঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেশ কয়েকমাস পর খোঁজ নিয়ে যান যতীন্দ্রনাথ। না, মেয়ের ওপর শ্বশুরবাড়িতে কোন অত্যাচার হচ্ছে না।
বাঘ মারার ঘটনাটি আলংকারীক; এই ঘটনাটি তাঁর নামের আগে একটি ‘বাঘা’নাম যুক্ত করেছিল হয়তো, তা বাঘ না মেরে যদি তিনি ডাইনোসর মারতেন তবে হয়তো তাঁর নামের আগে অন্য কোন অলংকার বসত। কিন্তু, তাঁর চরিত্রের যে বিশালতা, এই অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠায় বয়ান করা সম্ভব কিভাবে? এই বিশালতা তো মাপা যায় না, এ তো ‘Imponderable’, যা কোনমতেই মাপা সম্ভব নয়! কার এত স্পর্ধা যিনি এই চরিত্রটি সম্পর্কে এককথায় বলবেন- “‘বাঘা-যতীন’ মানে... যিনি বাঘ মেরেছিলেন না?”
আমেরিকায় ‘ফন্ পাপেন’ নামক জনৈক ব্যক্তির সাহায্যে কেনা অস্ত্রগুলি ‘অ্যানি লার্সেন’ নামক জাহাজে করে আসে প্রশান্ত মহাসাগরে। সেখানে ‘মাভেরিক’ জাহাজে অস্ত্রগুলি তোলা হয়। কিন্তু বাটভিয়াতে এই জাহাজ ব্রিটিশ নৌবিভাগের হাতে ধরা পড়ে। অপরদিকে ‘অ্যানি লার্সেন’-ও ধরা পড়ে যায় মিত্রশক্তির হাতে। ব্যাঙ্ককে সেইসময় ছিলেন ‘গদর’ কর্মীরা- ‘পাখো’ শহরের কাছাকাছি। মাল ডেলিভারি হলেই খালাস করে দেশে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু ‘অ্যানি লার্সেন’ ও ‘মাভেরিক’ নামক জাহাজদুটি ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়; হাতে-নাতে ধরা পড়ে যান তাঁরা।
ওড়িশার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে অপেক্ষায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথ; সঙ্গী চার শিষ্য- চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল(ডাক নাম- ‘চাক’)। সেইসময় জার্মান কাউন্সিল থেকে স্থির করা হয়, দুলাখ টাকা ও দুহাজার অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা হবে বালেশ্বর উপকূলে। সেই মাল খালাসের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন যতীন্দ্রনাথ। এই পরিকল্পনাও ভেস্তে যায় ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তৎপরতায়।৪ঠা সেপ্টেম্বর মধ্যরাতের ট্রেনে কোলকাতা থেকে বালেশ্বরে উপস্থিত হন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডেনহ্যাম। সাথে কমিশনার চার্লস টেগার্ট ও কয়েকজন সশস্ত্র পুলিস; বালেশ্বরে যতীন মুর্জ্জীর অবস্থানের ‘পাকা খবর’ পেয়ে। শিষ্যরা বারংবার অনুরোধ করেন যতীনকে, পালাবার পরামর্শ দেন। রাজি হন নি বীর, গর্জ্জে ওঠেন-
“… আমরা মরব। আমাদের বুকের তাজা রক্তে নেয়ে উঠবে স্বদেশের মাটি। সেই মরণ দেখে সমস্ত ব্যর্থতা ভুলে দেশের লোক ছুটে যাবে ভবিষ্যতের দিকে।”
৯/১১/১৯১৫। বুড়িবালামের তীরে রচনা হল ‘নবভারতের হলদিঘাট’। চষাক্ষেতের ওপর একটি টিলা। সেই টিলার আড়ালে সংগ্রামরত পাঁচ বিপ্লবী। বিপক্ষে অগুন্তি পুলিস। নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি ও সার্জেন্ট রাদারফোর্ড। প্রথমে ‘ফ্রন্টাল অ্যাসল্ট’-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টিলার ওপার থেকে অবিরাম গুলি ও নিজবাহিনীর হতাহতের বহর বাধ্য করল অবশিষ্ট পুলিসবাহিনীকে ধানক্ষেতের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে। টিলার ওপারে পুরোভাগে নেতৃত্বে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ডানহাতের কনুইতে গুলি লেগেছে। ডানহাত থেকে বামহাতে রিভলবার নিয়ে সমান দক্ষতায় গুলি চালাচ্ছেন তিনি। অদূরেই নিথর হয়ে পরে রয়েছে একটি দেহ- সেটি চিত্তপ্রিয়র। দলের কমবেশি সবাই আহত । সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল ‘অ্যামিউনিশনস’। ধরা দিলেন বিদ্রোহীরা। জ্যোতিষ পাল বুকে গুলি খান। চিত্তপ্রিয় শেষ। নীরেন আহত, রক্তাক্ত। একমাত্র অক্ষত মনোরঞ্জন। আর যতীন্দ্রনাথ? তলপেটে দুটি গুলি খেয়ে তিনি আসন্ন মৃত্যুর জন্য তৈরি। তাঁর মৃত্যু হয় পরদিন- বালেশ্বর গভর্ণমেন্ট হাসপাতালে। বিপ্লব আপাতত শেষ(?)।
ইনি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, পরবর্তীকালে লোকে যাকে চিনবে ‘বাঘা-যতীন’ নামে। ভুল বললাম, লোকে এঁকে চিনে নেবে বাংলার অবিসংবাদিত বিপ্লববাদের নায়ক হিসেবে, বুড়িবালামের তীরে চষাক্ষেতে যিনি রচনা করবেন ‘নবভারতের হলদিঘাট’। রচনা হবে গেরিলাযুদ্ধের এক নতুন কায়দা, যা ভবিষ্যতে অনুসৃত হবে ‘অলিন্দ যুদ্ধ’তে, জালালাবাদ বা অ্যালফ্রেড পার্কে; সর্বশেষে ব্রহ্মদেশের ‘ক্ল্যাং ক্ল্যাঙ্গ’ বা ‘টামু’র যুদ্ধে, হয়তো বা ‘পালোল’ বিমানবন্দরেও। যে মহানায়কের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করবেন তাঁর ‘অগ্রণী’ কবিতা, যার একটি স্তবকে তিনি বলবেন-
-“ওরে ক্ষ্যাপা, ওরে হিসাব ভোলা,
দূর হতে তাঁর পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধূলা
তোর আপন মরণ দিলি পেতে!
না দেখে না শুনেই তোদের বাঁধন পড়ল খ’সে
চোখে দেখার অপেক্ষাতে
রইলি নে আর বসে!”
[ক্রমশঃ]...






















![[সূর্যের অন্ধকার অর্ধ]](https://cdn.storymirror.com/cover/thumbnail/4c166cbabbbf0a8cebd486ded8bc474a690b7d42.png)