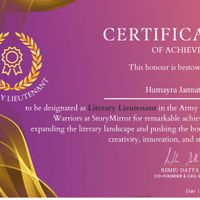তিন পাতার গল্প
তিন পাতার গল্প


চীনাবাদামের ঠোঙা হাতে মাঠের এককোণে গিয়ে বসলো প্রদীপ। মাঠে বাচ্চাদের জটলা, কিছু একটা খেলনা নিয়ে হইচই চলছে। বিকেলের সময় এই মাঠে বসে সময় কাটাতে প্রদীপের ভালো লাগে খুব। এখন মাধ্যমিকের পর অনেক ফাঁকা সময়। মোবাইল ঘেঁটে ঘেঁটেও একসময় বিরক্তি চলে আসে। আর খেলাধূলো দৌড়-ঝাঁপে তার কোনোদিনই বিশেষ উৎসাহ ছিলো না। তাই ঘাসে বসে-শুয়েই সময় কাটানো।
বাদামগুলো একে একে শেষ করে ঠোঙাটা ফেলে দিতেই যাচ্ছিলো প্রদীপ। কী মনে হতে ঠোঙাটার ভাঁজ খুলে ভাবলো কী আছে দেখা যাক। কবেকার কোন খবরের কাগজ কি কারও অঙ্ক খাতার পৃষ্ঠা দিয়ে বানানো - সেসব পড়তে বেশ একটা অন্যরকম মজা লাগে। ঠোঙাটা খুলে প্রদীপ দেখলো সেটা খবরের কাগজ নয়, কোনো গল্পের বইয়ের পাতা জুড়ে বানানো। ছোট গল্পের বই ছিলো নিশ্চয়ই। এই পাতাটা হলো একুশ আর বাইশ পাতা। একুশ পাতায় একটা গল্প শুরু হয়েছে, গল্পের নাম 'ভাঙ্গাবাড়ি'। আর লেখকের নাম আছে করুণাশঙ্কর রায়। কে তা কে জানে! খুব বিখ্যাত কেউ তো নয়ই। প্রদীপ কখনো নামই শোনেনি। সে গল্পটা পড়তে শুরু করলো।
গল্পটা একটা পুরোনো জমিদার বাড়ি নিয়ে। প্রথমে ভুতের গল্প মনে হলেও একটু পড়তেই বোঝা গেলো যে এটি আসলে একটি ছোট্ট রহস্য গল্প। আর গল্পে একটিই চরিত্র, তার নাম প্রদীপ। প্রদীপ বেশ মজা পেলো। এই প্রথম সে জীবনে এমন একটা গল্প পেলো যেখানে তার নামটাই গল্পে রয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, অনেকের নামের সঙ্গেই নিশ্চয়ই এরকম হয়। তবে প্রদীপ এই নামে কোনো চরিত্র আগে কোনো গল্পে পায়নি। যেহেতু নামটা এক, তাই পড়তে পড়তে যেন নিজেকেই গল্পের চরিত্র বলে মনে হতে লাগলো তার। প্রদীপ সেখানে পুরোনো একটি বাড়িতে একটি পৃষ্ঠা খুঁজে পায়। তাতে জমিদার বাড়ি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য এবং কিছু হীরের সন্ধান রয়েছে। কিন্তু পৃষ্ঠাটি ছেঁড়া। সেই ছেঁড়ার অবশিষ্ট অংশটা খুঁজে বার করা নিয়েই গল্প।
পড়তে পড়তে দ্বিতীয় পাতায় পৌঁছে হতাশ হলো প্রদীপ। গল্পটা বাইশ নম্বর পাতায় শেষ হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে আর সামান্য একটু বাকি। সেটা নিশ্চয়ই তেইশ নম্বর পাতায় ছিলো। কী আর করা যাবে। নিরুৎসাহ হয়ে বসে রইলো সে। তারপর হঠাৎই মনে হলো তার, একটা চেষ্টা করলে হয় না ? ওই তেইশ নম্বর পাতাটা খুঁজে বের করার। ঠিক যেমন গল্পের প্রদীপ উদ্ধার করছিলো ছেঁড়া কাগজটার বাকি অংশ।
যেমনি ভাবা, প্রদীপ উঠে দৌড়ে গেলো অদূরে দাঁড়ানো বাদামঅলার কাছে। বললো, তোমার ঠোঙাগুলো একটু দেখতে দেবে ?
বাদামঅলাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে তাকে রাজি করানোর পর প্রদীপ ঠোঙাগুলো একে একে দেখতে লাগলো। কোনো-কোনোটায় হরফ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা অন্য বইয়ের পাতা। কোনোটা আবার খবরের কাগজ কেটে বানানো। তিন-চারটে ঠোঙার হরফ একইরকম, ওই আগের বইয়ের পাতা কেটেই বানানো। কিন্তু একটা সাত-আট, একটা তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন, একটা সাতান্ন-আটান্ন, আর শেষতমটা পঁচিশ-ছাব্বিশ পাতা। প্রদীপ কৌতূহল নিয়ে পঁচিশ পাতার লেখাটা পড়লো। না - উপর থেকে পড়েই বোঝা যাচ্ছে এটা অন্য গল্প। গল্পের নাম এখানে লেখা নেই। বাহ্, তার মানে এই গল্পটা নিশ্চয়ই চব্বিশ নম্বর পাতায় শুরু হয়েছে। অর্থাৎ তার অনুমান সঠিক, ভাঙ্গাবাড়ি গল্পটা তেইশ পাতাতেই শেষ। সেই পাতাটা অবশ্য ঠোঙাগুলোর মধ্যে নেই। তবু এইটুকুতেই প্রদীপ বেশ খুশি হয়ে উঠলো নিজের বুদ্ধিমত্তার কথা ভেবে।
কিন্তু তেইশ নম্বর পাতাটা কী করে পাওয়া যায় ? প্রদীপ বাদামঅলাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি মনে করে বলতে পারবে এই মাপের ঠোঙা তুমি আজ ক'টা বিক্রি করেছো ?
বাদামঅলার বয়স অল্প, সতেরো-আঠেরো হবে। প্রদীপেরই সমবয়সী প্রায়। সে বললো, ওটা কুড়ি টাকার ঠোঙা। কুড়ি টাকার ঠোঙা খুব বেশিজন নেয় না, সবাই দশ টাকাই নেয়। সকাল থেকে আট-দশটার বেশি কুড়ি টাকা বিক্রি হয়নি। কিন্তু কখন কাকে কোন ঠোঙাটা সে দিয়েছে, সেসব তার অতো মনে নেই।
প্রদীপ ভাবলো, সেটা কোনো অসুবিধা হবে না। বাদামঅলা সকাল থেকে যেখানে যেখানে বাদাম বিক্রি করেছে, সেখানে গিয়ে দেখলেই হবে। লোকে বাদাম খেয়ে ঠোঙাটা তো মাঠের ধারে কিংবা রাস্তার ধারেই ফেলে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তেইশ-চব্বিশ নম্বরের পাতাটা আদৌ ওই আট-দশটা পাতার মধ্যে আছে কিনা।
থাক না থাক, প্রদীপ বাদামঅলাকে জিজ্ঞাসা করলো, সকাল থেকে তুমি কোথায় কোথায় বিক্রি করেছো বলো তো ?
বাদামঅলা যা বললো তাতে প্রদীপ আশান্বিতই হলো। জানা গেলো যে সকাল থেকে বাদামঅলা কাছাকাছিই একটা পার্কে ছিলো। তারই আশেপাশে যা বিক্রি হবার হয়েছে, সেখান থেকে সরাসরি সে এখানে এসেছে।
বাদামঅলাকে আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকতে বলে প্রদীপ দৌড় লাগালো সেই পার্কের দিকে। সেখানে পৌঁছে সে রাস্তার আশেপাশে পরে থাকা কাগজের মধ্যে তার তেইশ নম্বর পাতার সন্ধান করতে লাগলো। কিছুই যে পেলো না, তা নয়। আরো দু-চারটে অন্যান্য ঠোঙার সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট বইয়ের পাতায় তৈরী ঠোঙাও দু'চারটে পাওয়া গেলো। কিন্তু কোনোটাই তেইশ-চব্বিশ নয়। সবগুলো ঠোঙা পাওয়াও গেলো না বলে প্রদীপ কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলো না। অথচ এতক্ষণের মধ্যে ওই শেষ না-হওয়া কাহিনীর কৌতূহল এবং তা খুঁজে বার করার রোমাঞ্চ তাকে পেয়ে বসেছে। গল্পের প্রদীপ কি হীরের সন্ধান দেওয়া কাগজের বাকি অংশটা খুঁজে পেলো ?
আবার সেই বাদামঅলার কাছে ফিরে এসে প্রদীপ জানালো যে সে সবকটা ঠোঙা দেখতে পায়নি। বাদামঅলা একগাল হেসে বললো, তা কি আর পাওয়া যায় - কে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।
প্রদীপ জানতে চাইলো, এই ঠোঙা তোমার বাড়িতে কি আর আছে ? কোথা থেকে কিনে আনো তুমি এইসব ঠোঙা ?
কৌতূহল ভালো, কিন্তু অতি কৌতূহল ভালো নয় - এই কথাটা বোধহয় বাদামঅলাকে কেউ ভালো করে শিখিয়েছিলো। সে এতক্ষণে একটু বিরক্ত হয়েই বললো, না - আমার কাছে আর নেই। যা কিনে এনেছিলাম হপ্তাখানেক আগে, সেসব শেষ হয়ে আজ এইকটা ঠোঙাই ছিলো। আর ঠোঙা কি আমি একা কিনছি সেখান থেকে ? কত লোকে এসে কত ঠোঙা কিনে নিয়ে যাচ্ছে, কার কাছে কত খোঁজ করবে ? ছাড়ো তো !
এই বলে বাদামঅলা তার ঝাঁকা উঠিয়ে অন্যদিকে পা বাড়ালো।
বিফল মনোরথ হয়ে মাঠের একধারে এসে আবার বসে পড়লো প্রদীপ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কী একটা এসে যেন খোঁচা মারলো পিঠে। পিছন ফিরে প্রদীপ দেখলো কিছু কমবয়সী বাচ্চা খেলা করছিলো, তাদেরই একজনের একটা কাগজের তৈরী এরোপ্লেন এসে গোঁত্তা খেয়ে পড়েছে। প্রদীপ এরোপ্লেনটা তুলে ভাঁজের উপর একটা ফুঁ দিয়ে নিঁখুতভাবে সেটা উড়িয়ে দিলো বাচ্চাদের দঙ্গলটার দিকে।
একটু পরে আলো কমে আসতে সে উঠে হাঁটা লাগালো বাড়ির দিকে। একটা অনুসন্ধান অসমাপ্ত রয়ে গেলো তার। যাক গে, সন্ধ্যেবেলাটায় ছাদে খুব সুন্দর হাওয়া দেয় এই সময়। সেই উদ্দেশ্যেই বরং পা বাড়ালো প্রদীপ। যদিও মাথার মধ্যে তার তখনও সেই পুরোনো জমিদারবাড়ির ছবি ঘুরছিলো। গল্পের প্রদীপ এঘর ওঘর খুঁজে খুঁজে শেষে বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে এসে পৌঁছালো। কাঠের দরজার চৌকাঠে কিছু একটা টুকরো আটকে আছে সে দেখলো। এরপর কী হলো ? এর পরের টুকুনিই তো অসমাপ্ত রয়ে গেলো, প্রদীপের জানা হলো না।
যদি সে খুব অন্যমনস্ক না হতো, যদি তার চোখ পড়তো সেই এরোপ্লেনের কাগজটায়, তাহলে দেখতে পেতো সাদা পাতার উপরের দিকে চেনা-চেনা হরফে লেখা আছে -
"ছোটগল্পকার শ্রীযুক্ত করুণাশঙ্কর রায়ের এই অসমাপ্ত গল্পটিই তাঁর শেষ রচনা। যতদূর জানা যায়, লেখক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এটি লিখতে শুরু করেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। গল্পের প্রদীপ হীরের হদিস পেলো কিনা তা জানা যায় না। অসমাপ্ত গল্পটির এখানেই ইতি।"
পাতার ডানদিকের কোণায় পৃষ্ঠাসংখ্যাও লেখা ছিলো। তেইশ।
~ সমাপ্ত