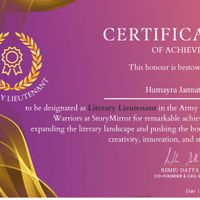কোলকাতার দুর্গা পূজা,কিছু তথ্য
কোলকাতার দুর্গা পূজা,কিছু তথ্য


দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ, উ কারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদস্মমতঃ। রেফো রোগঘ্ন বচনোগশ্চপাপঘ্নবাচকঃ, ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। দুর্গা’ শব্দের বর্ণ গুলির মধ্যে রয়েছে দেবীর স্বরূপ। দ- দৈত্য বিনাশের, উ- বিঘ্ননাশের, রেফ- সর্ব রোগ নাশের, গ- পাপ বিনাশের এবং আ- শোক, দুঃখ ও শত্রু বিনাশের সূচনা করে। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। অবশ্য এ ছাড়াও দুর্গা নামের আরো কিছু অর্থ পণ্ডিতদের কলমে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে।
সপরিবারে (কত্তা মশাই বাদে) মা দুর্গার সনাতন যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করে অভ্যস্ত তার বাইরেও আরো নানা রূপে তাঁর আরাধনা করা হয়। তাঁর অষ্টাদশ ভূজা, ষোড়শ ভূজা, অষ্ট ভূজা এবং চতুর্ভুজা মূর্তিও দেখা যায়।বাহনও কিছু কিছু অঞ্চলে সিংহের যায়গায় বাঘ বা ঘোড়া থাকে। নামে বা রূপে ভিন্নতা থাকলেও পুজোর এই কটা দিন কোন রকম ভিন্নতা ছাড়াই আমরাআনন্দ সাগরে অবগাহন করি। কোলকাতার পুজো চিরকালই সংখ্যায় আর জেল্লায় অন্যদের থেকে অনেকটা ওপরে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে প্রতিমা, আলো আর প্যান্ডেলের অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে।
১৬১০ সালে কোলকাতায় প্রথম দুর্গা পুজো করে বরিষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার। কারো কারো মতে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদার ১৬০০ সালে প্রথম দুর্গা পুজো করেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে তথ্যের সমর্থন অনেক বেশী। আজকের জৌলুস, আলোর ঝলকানি, নজর কাড়া বাহারি প্যান্ডেলের জোয়ারের মাঝে সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের পুজো আজও অনুষ্ঠিত হয় তার সাবেকিয়ানা বজায় রেখে। এ বড় কম কথা নয়। এরপর পাথুরিয়াঘাটায় রাম লোচন ঘোষ(১৭২৭), শোভাবাজারে রাজা নব কৃষ্ণ দেব(১৭৫৭), ভবানিপুর চক্রবেড়িয়ায় রাজা রামগোবিন্দ মিত্র(১৭৫৭), দর্জিপাড়ায় দয়ারাম দাঁ(১৭৬০), হেদুয়ায় রামদুলাল দে সরকার(ছাতুবাবুর পুজো নামে খ্যাত, ১৭৭০ মতান্তরে ১৭৮০), একে একে কলকাতার বিত্তবান মানুষজন দুর্গাপুজো নিয়ে মেতে ওঠেন। দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে শুধু যে নিছক আমোদ বা বিত্ত বৈভবের উগ্র প্রদর্শন হত তাই নয়, শোভাবাজারের মত কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইংরেজদের তোশামদের জন্যও বিনোদনের এলাহি ব্যবস্থা থাকত।
এরপর কেবলমাত্র ধনীরাই নয় ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষও দুর্গা পুজোনিয়ে মেতে ওঠে। কিন্তু কেবল মাতলেই তো হবে না, পুজো করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা তো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। পথ দেখাল হুগলীর গুপ্তিপাড়ার বারজন বন্ধু। ১৭৯০ সালে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা দুর্গা পুজোর আয়োজন করল। বার জন বন্ধু অর্থাৎ ইয়ার মিলে পুজোটি করেছিল বলে তা ‘বারোয়ারি’ আখ্যা পেল। সেই বারোয়ারি পুজোর সূচনা। এই ব্যাপারে কিন্তু কোলকাতা বেশ খানিকটা পিছিয়ে। কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ ১৮৩২ সালে বারোয়ারি পুজোর সাথে কোলকাতার পরিচয় করান। পুজোয় সাধারণ মানুষের সক্রিয় যোগদান ক্রমশ বাড়তে থাকায় আত্মপ্রকাশ করে সর্বজনীন দুর্গা পুজো। কোলকাতার প্রথম স্বীকৃত সর্বজনীন পূজা হয় ১৯১০ সালে। সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে বলরাম বোস ঘাট রোডে পুজোটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সর্বজনীন পুজোগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দেশাত্মবোধের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হত। স্বাধীন দেশে সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন বারোয়ারি আর বারোজনের পুজো নেই, সর্বজনীন এর সাথে সমার্থক হয়ে গেছে। সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে পুজোর সংখ্যা, কলেবর, বৈচিত্র। আর এখন তো থিমের যুগ। বড়, ছোট, মাঝারি, সব উদ্যোক্তাই তাদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসুত কিছু না কিছু থিমের ডালি নিয়ে হাজির হন।
এ তো গেল তত্ত্ব আর তথ্যের কথা। এবার আসি পুজোকে কেন্দ্র করে সেকালের কিছু ঘটনা ও রটনার প্রসঙ্গে।
সালটা ১৮৪০। ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া একটা পালকি চলেছে বেহালার দিকে। বেহালায় সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে বারোয়ারিতলাতে পা দেওয়া মাত্র হুকুম এল “পালকি থামাও”। বেহারারা থেমে গেল। হুকুমদারেরা সামনে এল।
-- সঙ্গে ব্যাটাছেলে কেউ নেই দেখছি। মাইজিকো বোলো রুপিয়া নিকালনেকো।
“ বেহারা কহিল, তাহাদিগের সঙ্গে কর্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই। এক কূল বধূ লইয়া যাইতেছে তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাঁহার সঙ্গে টাকা- পয়সাও নাই তবে, তাহারা টাকা কোথায় পাইবে।“
যুবক দল হো হো করে হেসে উঠল। সাবর্ণ চৌধুরীরা কয়েক বছর আগেও কোলকাতার মালিক ছিল। সেই অহং থেকেই ধমক এল—জানিস তো আমরা বেহালা চৌধুরী বাড়ির ছেলে। তোদের মাইজিকে বল, চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা যখন ধরেছে, তখন কিছু না দিলে ছাড়ান নেই। আঁচলের গিঁটখানা খুলে দিতে হলেও তারা নেবে। তোদের বধূকে বের কর, তাঁর সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কিনা আমরা দেখব।
“বেহারা কহিল, তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না, তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া বধূর মুখ দেখ”
ছেলেগুলো এটাই চাইছিল। মান্য বংশের বখাটে ছেলেরা চারিদিক থেকে ঘেরাটোপে তাদের নির্লজ্জ হাত দিল। ভেলভেটের আবরণখানা তুলতেই আনন্দে আটখানা মুখগুলো ভয়ে চুপসে গেল। পালকিতে বধূ বেশে বসে রয়েছেন ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেটন সাহেব। ফলত চাঁদা তো এলোই না, বেশ কয়েকজনের শ্রীঘরে ঠাঁই হল। “সমাচার দর্পণে” বেশ কিছুদিন ধরে বেহালার বারোয়ারি পাণ্ডাদের বিশেষ করে চৌধুরী বাড়ির ছেলেদের পথ চলতি মানুষের ওপর উপদ্রব নিয়ে লেখালিখি হচ্ছিল। পেটন সাহেব ছদ্মবেশে এসেছিলেন সেটাই নিজের চোখে পরখ করতে। তবে পেটন সাহেবের সাধ্য কি পুজোর অছিলায় অন্যের পয়সায় ফুর্তি করার এমন আয়োজন বানচাল করে। সেই বখাটে ছেলেদের উত্তরসূরি আজকের পুজোর বীরপুঙ্গবেরা কিন্তু আদর্শচ্যুত হয়নি। কেবল পালকির যায়গায় তারা ধরে লরি, আর এভাবেই হয়ত নিবেদন করে সমমনস্ক পূর্বসূরিদের প্রতি তাদের অন্তরের তর্পণ। আর একটি জিনিস লক্ষণীয়, অতকাল আগে ইতি উতি চাঁদার জুলুম যেমন ছিল তেমনই ছিল প্রশাসনিক তৎপরতা এবং বাংলা সংবাদপত্রের একেবারে ঊষা লগ্নেও লক্ষণীয় সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা।
সেকালের চাঁদা তোলা নিয়ে অনেকমজার গল্প শোনা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর এমনই একটি ঘটনা “হুতোমের” বয়ানে শোনা যাক।
‘একদল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধরে “ধরেছি” “ধরেছি” বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তার লোক জমে গ্যালো- সিংগি বাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বললেন, “মহাশয়! আমাদের অমুক যায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিংগির উপরে চড়ে কৈলাশ থেকে আসছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং, তিনি আর আসতে পার্চ্চেন না, সেই খানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোনমতে ছেড়ে দেব না- চলুন! যাতে মার আসা হয়, তাই তদ্ বির করবেন।“
সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।‘
বারোয়ারি গণতান্ত্রিক ব্যাপার। গণতন্ত্রে যদি দলাদলি চলে তবে বারোয়ারিতেও তা চলবে। ঘটনা অবশ্য কোলকাতার নয়, বাইরের। ১৮১৯ সালের খবর শুনুনঃ- ‘উলাগ্রামে উলাইচন্ডীতলা নামে এক স্থানে বার্ষিক চন্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক দক্ষিণ পাড়ায় মহিষ মর্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্য বাসিনী পূজা উত্তর পাড়ায় গণেশ জননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষা প্রযুক্ত আপন আপন পাড়ার পূজা ঘটা করিতে সাধ্য পর্যন্ত কেহই কসুর করে না।‘
আর একটি মজার ঘটনায় আসা যাক, এটিও কোলকাতার বাইরের।
হুতোম লিখছেনঃ ‘একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারো-ইয়ারি পূজা করেন, সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল। শেষ বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন করতে হয়েছিল, তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা মা’র অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোয়ারি পুজো করেন তাহাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।‘
আজকাল পুজোর ভাসানে মদ খাওয়াটা প্রায় অবশ্যকরণীয় একটি কাজ। পেটে একটু না পড়লে নাচার যোশ আসবে কি করে? আমাদের পূর্বপুরুষ জয় মিত্র এমনই একজন। অতি বিত্তবান, অতি মূর্খ এবং সুরাসক্ত। এনার নামে উত্তর কোলকাতায় একটি রাস্তা আছে। রকমারি নির্বোধ কাজের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তবে নির্বুদ্ধিতা নয় নেশাগ্রস্ত জয় মিত্রের কান্ড কারখানা দেখুন। প্যারিচাঁদমিত্রের “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়” গ্রন্থে নামোল্লেখ না করে সংক্ষেপে ঘটনাটি আছে। বিস্তারিত আকারে জানিয়েছেন ওনার পরবর্তী প্রজন্মের একজন—
‘বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে—বাবু চলেছেন পুরোভাগে। ঢাকি ঢুলিরাও চলেছে বাজাতে বাজাতে। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে দুটো বড় বড় নৌকো নেওয়া হল। একটায় ঊঠলেন বাবু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে, অন্যটায় ঢাকিঢুলি, বাজনদার, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদিরা উঠল। বিসর্জনের বাজনা বাজছে, মিত্রমশায়ের নেশাও তুঙ্গে উঠছে। দুটো নৌকোর মাঝখানে প্রতিমা ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।মাঝ গঙ্গায় গিয়ে নৌকো দুটো জোড় ভেঙ্গে দূরে সরে গেল, প্রতিমাও ঝুপ করে জলে পড়ল। এমন সময় মিত্তির মশায় হেঁকে উঠলেন “ওরে ব্যাটারা, তোরা এখনও নৌকায় দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছিস—মা যে কৈলাসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন—মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে খেয়াল নেই? যা যা যা—মার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আয় ব্যাটারা---।“
সাঙ্গপাঙ্গরা বাবুর মন রাখতে ঢাকিদের নৌকো দিল উল্টে। বেচারা ঢাকির দল ঢাক সমেত জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে পাড়ে গিয়ে উঠল’
উল্লিখিত ঘটানাগুলো আজ থেকে দেড়শ দুশ বা কোনটা তারো আগের। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এর অনেকটাই যেন আমাদের চেনা, জানা বা দেখা। এখনকার চিত্রনাট্যে শুধু জমিদারেরা নেই। সেই স্থান নিষ্ঠার সঙ্গে পূরণ করেছেন প্রতিপত্তিশালীরা। আজকের এই লাগামছাড়া বাজেটের পুজোয় পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজনও আছে, তা তাঁরা যে কারণেই পুজোর সাথে যুক্ত হোন না কেন।
শারদোৎসবের আনন্দমেলায় শুধু একটাই কামনা—কারো আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয়, কোন জয় মিত্রের লাগামছাড়া উল্লাস উদ্দীপনার কারণে যেন আর কোন ঢাকির প্রাণান্তকর অবস্থা না হয়।