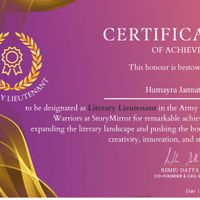গেরাম বাঙলার দুই পরব
গেরাম বাঙলার দুই পরব


ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে বাংলার ঘরে ঘরে সারারাত জেগে যেমন চলে রান্নাপুজোর আয়োজন তেমনই হয় আরেক মেয়ের আরাধনা। ভাদু উৎসব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার লৌকিক উৎসব।
ভাদু উৎসব নিয়ে মানভূম অঞ্চলে বেশ কিছু লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে। পঞ্চকোট রাজপরিবারের নীলমণি সিংদেওর তৃতীয়া কন্যা ভদ্রাবতী বিবাহ স্থির হওয়ার পর তার ভাবী স্বামীর অকালমৃত্যু হলে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন, এই কাহিনী মানভূম অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচারিত। বিয়ে করতে আসার সময় ভদ্রাবতীর হবু স্বামী ও তার বরযাত্রী ডাকাতদলের হাতে খুন হলে ভদ্রাবতী চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন করেন বলে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পুরুলিয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ভদ্রাবতীকে জনমানসে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নীলমণি সিংদেও ভাদু গানের প্রচলন করেন। কিন্তু এই কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত পঞ্চকোট ইতিহাস নামক গ্রন্থে এই ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। নীলমণি সিংদেও তিনজন পত্নীর গর্ভে দশজন পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেও তার কোন কন্যাসন্তানের ছিল কিনা সেই বিষয়েও সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে। বীরভূম জেলায় ভদ্রাবতীকে হেতমপুরের রাজার কন্যা হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। এই জেলায় প্রচলিত রয়েছে যে, ভদ্রাবতীর সাথে বিবাহ স্থির হওয়ার পর ইলামবাজারের নিকটে অবস্থিত চৌপারির শালবনে ডাকাতদের আক্রমণে বর্ধমানের রাজপুত্রের মৃত্যু হলে ভদ্রাবতী তার সাথে সহমরণে যান।
তবে শুধুমাত্র এটাই নয়, ভাদুপুজো নিয়ে নানা পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। ভাদুকে অনেকেই লক্ষ্মী হিসেবে পুজো করেন। বলা হয় শস্যের দেবী। ধান ওঠার পরই চাষিদের ঘরে তাই ভাদুর আরাধনা হয়।
পয়লা ভাদ্র কুমারী মেয়েরা গ্রামের কোন বাড়ীর কুলুঙ্গী বা প্রকোষ্ঠ পরিষ্কার করে ভাদু প্রতিষ্ঠা করেন। একটি পাত্রে ফুল রেখে ভাদুর বিমূর্ত রূপ কল্পনা করে তারা সমবেত কন্ঠে ভাদু গীত গেয়ে থাকেন। ভাদ্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে ভাদুর মূর্তি ঘরে নিয়ে আসা হয়। ভাদ্র সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রকে ভাদুর জাগরণ পালিত হয়ে থাকে। এই রাত্রে রঙিন কাপড় বা কাগজের ঘর তৈরী করে এই মূর্তি স্থাপন করে তার সামনে মিষ্টান্ন সাজিয়ে রাখা হয়। এরপর রাত নয়টা বা দশটা থেকে ভাদু গীত গাওয়া হয়। কুমারী ও বিবাহিত মহিলারা গ্রামের প্রতিটি মঞ্চে গেলে তাদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও তারা এই সব মঞ্চে ভাদু গীত পরিবেশন করে থাকেন। ভাদ্র সংক্রান্তির সকালে দলবদ্ধভাবে মহিলারা ভাদু মূর্তির বিসর্জন করা হয়।
ভাদু গীত
পঞ্চকোট রাজপরিবারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজদরবারে হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ, তবলা, সানাই সহযোগে মার্গধর্মী উচ্চ সাহিত্য গুণ নির্ভরএক ধরনের ভাদু গাওয়া হত হয়। এই পরিবারের ধ্রুবেশ্বরলাল সিংদেও, প্রকৃতীশ্বরলাল সিংদেও এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও দরবারী ভাদু নামক এই ঘরানার সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু অন্যান্য সকল ভাদু গীত লৌকিক সঙ্গীত হিসেবেই জনপ্রিয় হয়েছে। লিখিত সাহিত্য না হওয়ায় এই গান লোকমুখেই প্রচারিত হয়ে এসেছে। টুসু ও ঝুমুর গানের বিপরীতে ভাদু গানগুলিতে প্রেম এবং রাজনীতি সর্বোতভাবে বর্জিত। সাধারণতঃ গৃহনারীদের জীবনের কাহিনী এই গানগুলির মূল উপজীব্য। পৌরাণিক ও সামাজিক ভাদু গানগুলি বিভিন্ন পাঁচালির সুরে গীত হয়। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণ-রাধার প্রেম পৌরাণিক গানগুলির এবং বারোমাস্যার কাহিনী সামাজিক গানগুলির বিষয় হয়ে থাকে। এছাড়া চার লাইনের ছড়া বা চুটকি জাতীয় ভাদু গানগুলিতে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতির চিত্র সরস ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা হয়। মূলত পাঁচালির সুরেই চার লাইনের ভাদুগান গাওয়া হয়। সারারাত জেগে গান গাওয়ার পর শেষ রাতে সকলে মিলে ভাদুকে বিসর্জন দিতে যান। সেই সঙ্গে করুণ সুরে সকলে গেয়ে ওঠেন...
'ভাদু যায়ো না জলে
কোলের ভাদু যায়ো না মোদের ছেড়ে
গটা ভাদর থাকলে ভাদু গো
মা বলে ত ডাকলে না
যাবার সময় রগড় লিলে
মা বিনে ত যাব না'।
মানভূমে নিম্ন সম্প্রদায় ও দরিদ্র মানুষের ঘরে ভাদু বেশি সমাদৃত। ১৭, সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ এবিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নটি সত্যিই ভাবিয়ে তোলে আমাদের ; পঞ্চকোটের রাজারা তাদের রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে বসতি দিয়ে বসবাস করলেও ভাদু নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরে বেশি সমাদৃত কেন?
তথ্যসূত্র:--১. আনন্দবাজার পত্রিকা ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট ; ২. বাউড়ি সমাজ
টুসু
পৌষ সংক্রান্তির দিন এক বিশেষ পরব হয়। মকর পরব বা টুসু পরব নামে পরিচিত। মকরের পরবের জন্য ইতিমধ্যেই টুসু বেচা কেনা শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। টুসু উত্সবের শেষ চারদিন চাউড়ি, বাউড়ি, মকর, আখান বলা হয়।
টুসু পূজা শুরু হয় অগ্রহায়ন সংক্রান্তির পরের দিন থেকেই। মাটির সরাকে চাল গুঁড়ো মাখিয়ে, তূষ ভর্তি করে তার উপর গোবর, দুর্বা প্রভৃতি ছড়িয়ে টুসুর প্রতিমূর্তি হিসেবে একটি পিঁড়িতে স্থাপন করা হয়। বাড়ির অবিবাহিতা মেয়েরা প্রতিদিনই একটি করে ফুল অঞ্জলি দেয় টুসুমাতার উদ্দেশ্যে – কোনো দিন গাঁদা, কোনো দিন আকন্দ আবার কোনো দিন বাসক ফুল। তারা তুলসী মঞ্চের পাশে গর্ত খুঁড়ে বা অস্থায়ী প্রকোষ্ঠ বানিয়ে পূজার ফুল জমিয়ে রাখে। হর দিন সন্ধ্যা নামলেই পূজারিণীরা সমবেত কন্ঠে গেয়ে চলে,
” তিরিশ দিন রাখি মা’কে,তিরিশটি ফুল দিয়ে গো/
আর রাখতে লারব মাকে, মকর আলো লজিকে।”
এভাবে এক মাস পর আসে টুসু জাগরণের রাত, পোষাকি নাম বাঁউড়ি। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ভাড়া করা ছোট ছোট লাউড স্পীকারে সার রাত ধরে চলে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির পেঁ- পোঁ! পৌষালি রাতে পাড়ার মেয়ে, বউরা সুরের মূর্চ্ছনায় জাগিয়ে রাখে রুখামাটির দেশকে। টুসু গীতের ছত্রে ছত্রে বিধৃত রয়েছে কতই না বেদনা বিধুর কাহিনী, সমকালীন সমাজচিত্র- কখনো আবার ধ্বনিত হয় অন্যের টুসুর প্রতি বক্রোক্তি-
“আমার টুসু মুড়ি ভাজে, চুড়ি ঝলমল করে গো/
উয়ার টুসু হ্যাংলা মিয়া, আঁচলা পাতে মাগে গো!”
পরের দিন মকর সংক্রান্তি। গানে গানে টুসু নিরঞ্জন। রঙীন সুদৃশ্য চৌড়লে চাপিয়ে টুসুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বড়ো জলাশয় বা নদীতে। সবেধন নীলমণি কন্যারত্নটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার সময়, গ্রাম্য রমণীদের সে কি শোকবিহ্বল চেহারা! অশ্রুসিক্ত বদনে তখন সেই মন খারাপের গান-
“আমার বড়ো মনের বাসনা/
টুসুধনকে জলে দিবো না”
শিলাই, কাঁসাই, সুবর্ণরেখার ঘাটে ঘাটে তখন কন্যা বিদায়ের আবেগঘন জলচিত্র-
“কাঁদছ কেনে সাধের টুসু, বড়ো দাদার হাত ধরে/
ই সংসারে বিটি ছেল্যা, রহে কি বাপের ঘরে!”
পরের দিন আখান যাত্রা। লোকে শুধায়, ‘পরব তোমার নাম কি?’- আমরা বলি, ‘নামেণ পরিচয়’। সেই সেদিন থেকেই যে সূর্যের উত্তরায়ন শুরু! সূর্যের গতির দিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে-( অর্ক> অর্কন> আখাইন> আখান) আখান যাত্রা! প্রথাগত শিক্ষায় প্রায় অশিক্ষিত মানুষদের অবাক করা জ্যোতির্বিদ্যা দক্ষতার আভাস পাওয়া যায় কুড়মালি ক্যালেন্ডারে। সূর্যদেবের যাত্রার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই আখানের দিনই হল আদিবাসীদের নববর্ষ। এদিন সকালে আড়াই পাক লাঙল চালিয়ে ‘হাল পুণ্য’র মাধ্যমে নতুন বছরের শুভ সূচনা, দুপুরে দইচিড়ে ভোজনান্তে দেবীর সমীপে চিরায়ত প্রার্থনা, -“আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে”। বর্ষবরণ উদযাপন করতে চাপাইসিনি, দুয়ারসিনি, দেউলঘাটাতে ধমাকেদার মেলা বসে। মেলায় ছৌ, ঝুমুর, নাচনি , বুলবুলি নাচ, ঘোড়া নাচ, নাটুয়া নাচ, মোরগ লড়াই উল্লেখযোগ্য ।
তথ্যসূত্র : http://www.voiceofchotanagpur.com/tusu-is-pride-of-manbhum/