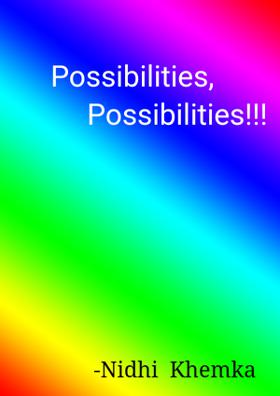বিশ্বাসঘাতক
বিশ্বাসঘাতক


সাবেক উত্তর কলকাতার তস্য গলির ভেতর একটা পুরানো বেশ ভাঙ্গাচোরা বাড়ির একতলায় হেমেশরা বহু বছর ধরে ভাড়ায় আছে। থাকতে থাকতে শিকর বাকর বিস্তার করে প্রায় বাড়ির মালিকই হয়ে বসেছে এখন। বাড়ির মালিক ধর্মদাস দত্ত হলেন একজন আদ্যোপান্ত সেয়ানা গোছের লোক, কিন্তু বাড়ি ভাড়া দেবার সময়ে সদ্য বাংলাদেশ থেকে আগত হেমেশদের থেকে মোটা টাকা নিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়েই ফ্যাঁসাদে পড়ে গেছেন। তখন শুধু হেমেশের দুই দাদা এসে বাড়িটা ভাড়ায় নিয়েছিল, পরে এক এক করে দেশ থেকে আরো এক অবিবাহিত দাদা, এক বাল্য বিধবা দিদি, হেমেশ সকলে মিলে এসে পুরো জাঁকিয়ে বসেছে। আর শুধু জাঁকিয়ে বসেই ক্ষান্ত থাকেনি, একদম পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে বাড়িওয়ালা থেকে অন্যান্য ভাড়াটে এমনকি পাড়া প্রতিবেশীদেরও অস্হির করে তুলেছে। বাড়িওয়ালার প্রধান সমস্যা হল, সেই যে একবার মোটা টাকা নিয়েছিলেন তারপর থেকে আর বাড়িভাড়া একটি টাকাও বাড়ায়নি হেমেশরা, উল্টে সময় মতো ভাড়া চাইতে গেলেও বাড়িওয়ালাকে পোষা নেড়ির তাড়া খাওয়ায়। বাড়ির উঠোন সহ অন্যান্য ফাঁকা জায়গায় হেমেশের দুই বিবাহিত দাদার খান ছয়েক ছানাপোনা দাপিয়ে বেড়ায়। মোটের ওপর বেশ জমজমাট ব্যাপার স্যাপার।
এদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার সাবেক এদেশীয় এমনকি পূর্ববঙ্গীয় অন্যান্য পরিবারের লোকজনও এড়িয়ে চলেন। এড়িয়ে চললেও কি আর তারা ঝগড়া থেকে দূরে থাকতে পারেন? এরা কিছু একটা নিয়ে ঠিক ঝামেলা করবেই করবে। আর হেমেশের দিদির বড় নাকটা সব বাড়ির রান্নাঘরের খবর নেবেই নেবে। তবে এদের মধ্যে হেমেশ ছোট থেকেই একটু অন্যরকম- মানে বাকিদের মতো কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধায় না, তাই ওর সাথে পাড়ার ছেলেদের অল্প বিস্তর মেলামেশা আছে।
হেমেশের তিন দাদার মধ্যে বড়জন অবিবাহিত ও বেকার, মেজো জনের একটা পান-বিড়ির গুমটি আছে, ছোটজন একটা ওষুধের দোকানে কাজ করে। ছানাপোনা নিয়ে ওদের পরিবারে জনা তেরো সদস্য দুটো ঘর আর একটা বারান্দায় ঠাসাঠাসি করে থাকে। সকাল থেকে নিজেদের মধ্যে হল্লা-চিল্লা করে। হেমেশ তখন পাড়ার ক্লাবের সামনের পৈঠায় বসে পড়াশোনা করে।
এরমধ্যে একদিন কিভাবে যেন হেমেশ সরকারী অফিসে কণিষ্ঠ কেরানীর চাকরি পেয়ে গেল। আর ওদের বাড়ির সকলের বিশেষতঃ দুই বৌদির নয়নের মনি হয়ে উঠল।
পাড়ার অন্যান্য বেকার বা সাকার ছেলেদের চোখের সামনে দিয়ে চিনে দোকানের চকচকে পালিশের জুতো, ধর্মতলার ফুটপাথের থেকে কেনা স্যুট-টাই পরে, হাতে বিশাল বড় টিফিন ক্যারিয়ার ঝুলিয়ে যখন হেমেশ গটমট করে অফিস যেতে শুরু করল; সে এক আশ্চর্য দৃশ্য হল| প্রায় ছ ফুট লম্বা, সিড়িঙ্গে, তেল চুকচুকে মাথা, কুচকুচে কালো চেহারার হেমেশকে হেঁটে যেতে দেখে মনে হত পুরো হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোট হেঁটে যাচ্ছে। কিছু দুষ্টু ছেলে পেছন থেকে ‘হ্যাঙ্গারে কোট’ বলে আওয়াজ দিলেও ও পাত্তা দিতনা।
বলাই বাহুল্য, হেমেশের সরকারি চাকরি পাওয়ার দৌলতে ওদের পুরো পরিবারের বেশ কিছু সুরাহা হল, দুই বৌদিকে মাঝে সাঝে ফেরিওয়ালাদের থেকে এটা সেটা কিনতেও দেখা যেতে লাগল।
হেমেশের বুড়ি দিদি এবারে হেমেশের বিয়ে দেওয়ার জন্য তেড়েফুঁড়ে উঠল। বৌদিরাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাত্রী খুঁজতে শুরু করল। পাড়া- প্রতিবেশী, খবরের কাগজ থেকে ঘটক কিছুই বাদ গেলনা। যদিও হেমেশদের সব পাত্রীকেই পছন্দ হয়, তবুও পাত্রীপক্ষরা হয় ওদের দুই ঘরের সংসার বা হেমেশের চেহারা কিছু একটা দেখে পালিয়ে যায়। এরকম উপযুক্ত পাত্রর বিয়ে না হলেও পাড়ার আধা বেকার বা অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের ছেলেদের টপাটপ নাকের ডগা দিয়ে বিয়ে হয়ে যেতে লাগল।
পাড়ার প্রতিটা বিয়ে বাড়ি গিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে হেমেশের দিদি বলতে লাগল যে, সামনের মাসেই নাকি হেমেশের বিয়ে। লোকজন আড়ালে এই নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করত। এইভাবেই হেমেশের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। হেমেশের দিদি আরো বৃদ্ধা হয়ে গেল আর পাত্রী দেখাও কমে এল। বৌদিরা স্বাভাবিক ভাবেই মন থেকে চাইতনা পরিবারে আরো একটা সদস্য বাড়ুক, তাছাড়া হেমেশের রোজগারের টাকাও তো দরকার ছিল সকলের।
এরমধ্যে হঠাৎ একটা বিয়ে বাড়ি গিয়ে হেমেশের দিদি আবার বলে বসল যে, সামনের মাসেই নাকি হেমেশের বিয়ে! পাড়ার লোকজন পুরানো কথা মনে করে আমোদে মেতে উঠল।
কিন্তু, এবারে যে হেমেশর দিদি ভুল বলেনি তা কিছু দিনের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেল। বেশ কয়েকজন নতুন লোকজনের বেশ ঘনঘন আগমন ঘটতে লাগল ওদের বাড়িতে। আশেপাশের বাড়িতে হেমেশের বৌদিদের আর দিদির মাধ্যমে মৌখিক নিমন্ত্রণও হয়ে গেল, আরও শোনা গেল সেই বউও নাকি সরকারি চাকরি করে! আবার সে ইংলিশেই বেশি স্বচ্ছন্দ। এরপরে শুরু হল আসল মজা। হেমেশ সবার সাথে দেখা হলেই ‘গুড মর্নিং’, ‘গুড ইভিনিং’ ইত্যাদি বলে মাথা খারাপ করে দিতে শুরু করল। একদিন দেখা গেল তার বেয়াদপ ভাইপোকে পড়া না পারার জন্য ঘেঁটি ধরে নর্দমায় মাথা ডোবাচ্ছে আর তুলছে, মাঝে মাঝে বলে উঠছে খাপছাড়া কিছু ইংরাজী শব্দ। প্রবীণ ঘোষবাবু আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, “আরে হেমেশ করো কি? ছেলেটাকে মারবে নাকি?” তার উত্তরে হেমেশ বলে উঠল, “নো নো, দিস ইস পচা ফুল”!
দিন যেতে লাগল আর হেমেশদের পুরো পরিবারের লোকজনের ইংরাজীর ঠেলায় পাড়ার লোকেদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল।
সকলে দাঁতে দাঁত চেপে নতুন বৌয়ের দেখা পাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।
অবশেষে সেই দিন এসে গেল। পাড়ার লোকেদের নাকের ডগা দিয়ে হেমেশ ফুলে ঢাকা গাড়ি চড়ে বিয়ে করতে চলে গেল।
যখন বৌ নিয়ে ফিরল, সকলে অবাক হয়ে দেখল তাল ঢ্যাঙা, কালো কুচকুচে হেমেশের পাশে ওর আর্ধেক উচ্চতার প্রচন্ড ফর্সা বৌ টুকটুক করে বাড়িতে ঢুকে গেল। উৎসাহী পাড়ার বৌ-মেয়েরাও সুযোগ পেয়ে পেছন পেছন ঢুকে গেল ওদের বাড়ি। সকলকে হেমেশের দিদি নতুন বৌয়ের গান শুনে যেতে অনুরোধ করল।
সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল, ছোট ছোট হাতে হারমোনিয়ামের বেলো টিপে বৌ হেঁড়ে গলায় গান ধরল, “আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।” নতুন বৌয়ের মুখে এই গান শুনে সকলে বুঝল যে হেমেশকে বিয়ে করে বৌ খুবই দুঃখিত। নাহলে এমন গান কেউ নতুন বিয়ের পর করতে পারে?
কদিন যেতেই সকলের চিন্তা ভাবনা কে ভুল প্রমাণ করে দুজনে হাত ধরে হাতে দুটো বিশাল বড় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে একসাথে অফিস যেতে শুরু করল।
বাড়িতে ঝগড়া শুরু হলেই নতুন বৌয়ের হেঁড়ে গলায় ‘স্টপ’ শুনে সবাই চুপ করে যেত। সাহস পেয়ে ওদের বাড়ির পাঁচিলে কাক, চিল এমনকি বিড়ালও বসতে শুরু করল। বৌদিদের আর দিদির মুখ চিন্তায় শুকিয়ে গেল। কদিন পরে শোনা গেল নতুন বৌ সবাইকে একঘরে ঠুসে দিয়ে আলাদা সংসার পেতেছে। আবার রাঁধুনীও রেখেছে একজন!
বছর ঘুরতেই ফিসফাস শোনা গেল নতুন বৌয়ের বাচ্চা হচ্ছেনা। আবার বৌদিদের হাসিমুখ দেখা গেল। পাড়ায় সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৌয়ের নিন্দে করতে শুরু করল সকলে।
নাহ্, সেই বৌকে কেউ কিছুতে হারাতে পারেনি। একদিন হঠাৎ, হেমেশ আর বৌ কোথাও পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ঘুরতে গেল। তার ঠিক তিন মাসের মাথায় একটা ছোট ছেলে কোলে করে ফিরে এসে পাড়াতেই সদ্য গজানো ফ্ল্যাটবাড়ি কিনে উঠল। মাঝে মাঝে হেমেশকে পুরোনো ভাড়া বাড়িতে দেখলেও বৌকে ওদিকে যেতে দেখা যেতনা কখনো। রাঁধুনীর সাথে সাথে বাচ্চার জন্য আয়া ঠিক করা হল। মাঝে মাঝে ফ্ল্যাট থেকে হেমেশের বৌয়ের হেঁড়ে গলা শোনা যেত। সে সবসময়ে ছেলেকে ইংরাজীতেই আদর করত, যদিও সেই ইংরাজী খুবই দুর্বোধ্য| আর সেই ছেলেকে কখনো পাড়ায় মিশতে দেখা যেতনা। একটু বড় হতেই কলকাতার নামকরা ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে কিভাবে যেন ছেলেকে ভর্তি করে দিল ওরা। এবারে হেমেশের বৌয়ের গলায় মাঝে মাঝেই শোনা যেতে লাগল, “বাবা আমার ওয়ানে পড়ে, এরপর টু তে উঠবে, তারপর বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে।”
কদিন পরে আর বৌয়ের বা হেমেশের গলা শোনা যেতনা। তার বদলে ছেলের গলাই শোনা যেতে লাগল, সবই কাজের লোকেদের আর বাবা-মা কে উদ্দেশ্য করে রাগের কথা। একদিন শোনা গেল প্রচন্ড উচ্চমানের উচ্চারণে, “আই উউল কিল ইউ, ও কে?” বাচ্চার গলায় এই কথা শুনে পাড়ার লোকজনেরও বুক কেঁপে উঠল।
এর কদিন পরেই ওরা ফ্ল্যাট বেচে কোথাও চলে গেল। শোনা গেল যে ওরা কোনো বিত্তশালী পাড়ায় বাড়ি কিনেছে ছেলেকে ভালো পরিবেশে মানুষ করার জন্য।
দিনে দিনে হেমেশের দাদারাও বাড়িওয়ালার থেকে কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেল। সকলের কাছে ওদের স্মৃতিও ফিকে হয়ে এল।
হঠাৎ একদিন হেমেশের সমবয়স্ক পুরোনো পাড়ার একজন ভদ্রলোকের দেখা হল ধর্মতলায়। হেমেশ নাকি অবসর নিয়েছে কাজ থেকে। একটা ছেঁড়া কোট পরে ফাটা চটি পরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় ঘুরছে। পুরোনো প্রতিবেশীকে জানিয়েছে, ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে লোন নিতে হয়েছিল বলে হাতে টাকা পয়সা অবসরের সময়ে প্রায় কিছুই পায়নি। আর ছেলের যাদের সাথে মেলামেশা তাদের উপযুক্ত ইংরাজী না বলতে পারার জন্য হেমেশ আর তার বৌ ফ্ল্যাটটা ছেলেকে দিয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে। দুজনের পেনশনের টাকায় কোনরকমে চলে যায়। আর ওর বৌ নাকি ইংরাজী বলা ছেড়ে দিয়েছে!
বিদায়ের সময়ে হাত নেড়ে হাসিমুখে পুরোনো পাড়ার বন্ধুকে হেমেশ বলেছে, “বাংলায় ফিরে এস বাবা।“