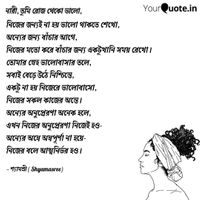কালাপাহাড়
কালাপাহাড়


সঠিক স্থান জানার প্রয়োজন নেই আমাদের। এই কাহিনীর স্থান কাল পাত্র নির্দিষ্ট এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। তা বহুধাবিভক্ত। সময় স্বাধীনতার কিছু আগে। রাতের গ্রাম বাংলা। ক্ষেতের মধ্যের অলিগলি সরু আলপথ দিয়ে দৌড়োচ্ছে এক ক্ষীণকায় যুবক, প্রাণভয়ে। কারণ তার পিছনে হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে আসছে একদল লোক, তাকে কুপিয়ে শেষ করবে বলে। ঘটনাটা খুব সাধারণ। খুঁজলে দেখা যাবে এরকম এখনো, এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আকছার হচ্ছে। এক্ষেত্রে কারণ হয়ত বা বেশ গুরুতর। এই যুবক মুসলিম। পাশের গাঁয়ের এক উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের মেয়েকে সে ভালোবাসত। তাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। তারপর যা হয় আরকি! এরা সব মেয়েটির কুটুম্ব, অকুটুম্ব লোকজন। হয়ত খুব একটা তফাৎ হত না চেনা ছকে, ছেলেটাকে ওরা শেষ করে দিত খুব সহজেই, কিন্তু পারেনি। কেন পারেনি তা জানতে হলে যেতে হবে ফ্ল্যাশব্যাকে।
ষোড়শ শতকের কথা। বাংলায় তখন সুলতানি সাম্রাজ্য। গৌড়ের সুলতানের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। তাঁর এমন নামের পিছনে রয়েছে ইতিহাস। সেকথায় পরে আসছি। আগে কিছু কথা বলে নিই তাঁর সম্পর্কে। ভদ্রলোকের আসল নাম ছিল রাজীবলোচন রায়। হিন্দু ছিলেন, বিশেষ কারণে, সম্ভবত আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এক মুসলিম মেয়ের সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর হাতে জলপান করেন। কিন্তু এই ঘটনা সমাজ মেনে নেয় নি। তখনকার হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা বিধান দেন তাঁর জাত গেছে। তিনি অনেক অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। এদিকে ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও ছোট থেকেই রাজীবলোচনের অস্ত্রশিক্ষার দিকে ঝোঁক ছিল, শিখেছিলেন অস্ত্রবিদ্যা। হিন্দু সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজের উপরই ক্ষেপে যান। গৌড়ের সুলতানের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তারপর তিনি দিকে দিকে হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন এবং হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করেন। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের উপর তাঁর ক্ষোভের শেষ ছিল না। তাঁর চরম নৃশংসতার জন্য তাঁর নাম হয় কালাপাহাড়। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি আসলে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন। তাঁর পন্থা ঠিক ছিল না হয়ত, কিন্তু তিনি বাংলা থেকে জাতিধর্ম ভেদাভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। তিনি নবদ্বীপ আক্রমণ করেও যখন চৈতন্যদেবের মানবপ্রেম ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শোনেন, তখন পিছিয়ে এসেছিলেন। তবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করেন, কারণ সেখানে ধর্মবিদ্বেষ ছিল প্রবল। দুর্দান্ত এই কালাপাহাড় ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতানের হয়ে মুঘল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোপের আঘাতে মারা যান।
এই পর্যন্ত বলে একটু জল খেয়ে দম নিতে থামলেন প্রফেসর আলী, ইউনুস আলী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। আমরা সব তাঁরই ছাত্র।
'তারপর কি হল প্রফেসর?' আমাদের সমস্বরে প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর আলী আবার শুরু করলেন। সেই যে আলপথে দৌড়োতে থাকা ছেলেটি, সে ছিল আমার নানা। সেদিন যদি তাঁকে কুপিয়ে মেরে ফেলত ওরা, তাহলে এই গল্প বলার জন্য আমায় আজ আর এখানে পেতে না। কাষ্ঠহাসি হাসলেন প্রফেসর। দৌড়োতে দৌড়োতে নানা হোঁচট খেয়ে পড়তেই ওরা প্রায় তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল। মৃত্যু আসন্ন ভেবে নানা যখন চোখ প্রায় বুজে ফেলেছেন, এমন সময় কিছু একটা দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল ওই লোকগুলো। নানা চেয়ে দেখলেন, মিশকালো এক ঘোড়ার পিঠে চেপে হাতে খোলা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক যোদ্ধা। জমকালো আলখাল্লা, গালে গালপাট্টা, মাথায় এদেশি টুপি, তাগড়াই চেহারা। এবার তিনি তরবারি হাতে ঘোড়া নিয়ে ওদের দিকে তেড়ে যেতেই ওরা এলোপাথাড়ি পালিয়ে গেল। ফিরে এসে ঘোড়া থেকে নেমে তিনি নানাকে তুলে ধরলেন। ঘোড়ার পিঠে করে নানাকে গ্রামের সীমানা পার করে দিয়ে এলেন। নানা তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেছিলেন তাঁর নাম রাজীবলোচন রায় বা রাজু। লোকে তাঁকে কালাপাহাড় বলে জানে।
এই কথা বলে তিনি আর দাঁড়াননি। হতভম্ব নানাকে পিছনে ফেলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিগন্তে হারিয়ে যান। পরে নানা খোঁজ করে জানতে পেরেছিলেন কাছাকাছিই সেই জায়গা, যেখানে কালাপাহাড় ওরফে রাজীবলোচন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিলেন। তাহলে নানার প্রাণদাতা আসলে কে? সে কোথা থেকে এসেছিল? কোথায়ই বা গেল? সে কি সত্যিই কালাপাহাড়? এসবের উত্তর বলাবাহুল্য নানারও জানা ছিল না। পরে দেশভাগের সময় নানা ঢাকায় চলে আসেন। তখন থেকেই আমরা ঢাকায় আছি। নানার মুখে যেমন শুনেছি অবিকল তেমনই তোমাদের শোনালাম। বিশ্বাস করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছে। এই কাহিনী আমি কাউকে শোনাই না, নেহাত আজ পড়াতে গিয়ে কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ল তাই। কালাপাহাড়কে সবাই মন্দির ধ্বংসকারী, হিংস্র লুটপাটকারী আখ্যা দিয়েছে, এগুলো তিনি সত্যিই করেছিলেন, কিন্তু আমাদের পরিবারের কাছে তিনি প্রাণদাতা। এই কথা বলে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ইউনুস আলী। ক্লাস শেষের ঘন্টা বেশ কিছুক্ষণ আগেই পড়ে গিয়েছিল।